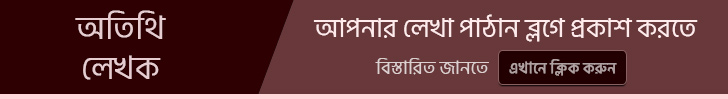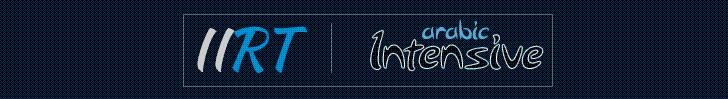এমন না যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার খুব স্মরণীয় বরণীয় কোনো স্মৃতি আছে। সেভাবে চিন্তা করলে মানুষের পুরো জীবনটাই নানারকম স্মৃতির সমষ্টি, ভার্সিটি লাইফ সেখানে আলাদা কিছু না। কিন্তু মানুষ নিজেকে নানা বিষয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ভাবতে পছন্দ করে। জাহাঙ্গীরনগরে ৬ বছর (সেশনজট না থাকলে ৫ বছরে শেষ হয়ে যেত অবশ্য) কাটানোর পর আমিও নিজেকে অব্যক্ত অনেক জ্ঞানের ভাণ্ডার বলে ভাবা শুরু করেছি, যা কারো সাথে শেয়ার না করলে ভালো লাগছিল না। আশা করি ভবিষ্যতে জাহাঙ্গীরনগরে নিজেকে অথবা সন্তানকে ভর্তি করাতে চাইলে আপনি এই লেখা থেকে উপকৃত হবেন।
এই লেখায় স্মৃতিচারণের চেয়ে বেশি থাকবে আমার কিছু মূল্যায়ন ও মন্তব্য। এগুলো লেখাটাই মূল উদ্দেশ্য, স্মৃতিচারণটা কেবল ছুতো। জাহাঙ্গীরনগরের বিভিন্ন বিষয়কে ইনসাইডাররা যেমন আজাইরা গ্লোরিফাই করে, আউটসাইডাররাও জাহাঙ্গীরনগরের অনেক বেইনসাফি সমালোচনা করে। একজন ইনসাইডার হিসেবে তাই আমি নিজের অবজার্ভেশানগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমি এগুলোকে নিরপেক্ষ বলে দাবি করি না। আমিও কোনো না কোনো ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রভাবিত। আমার লেখায় তাই এগুলোর প্রতি বায়াস থাকবেই।
লেখাটি যখন টাইপ করতে শুরু করেছি, তখনও আমি এর বিষয়বস্তুর বিন্যাস নিয়ে কনফিউজড। হল লাইফের আলোচনা করতে গেলে এর মধ্যে র্যাগের আলোচনা চলে আসে, আবার র্যাগ আলোচনা করতে গেলে তাতে স্টুডেন্ট পলিটিক্স চলে আসে। অথচ সবগুলোকে আমি আলাদা আলাদা পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করতে চাচ্ছিলাম। আবার দেখলাম লেখাটি অকল্পনীয় রকমের বড় হয়ে যাচ্ছে। কয়েক পর্বে লিখতে হবে। পরে ভাবলাম গুরুত্বের বিচারে প্রথম পর্বে হল লাইফ আর র্যাগিং নিয়ে আলোচনা করি। তবুও কিছুটা বড় হয়ে যায় বলে শুধু হল লাইফ আলোচনা করলাম। আল্লাহ তাওফীক দিলে পরের পর্বগুলোতে অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।
হল লাইফ
ছাত্রাবাসকে ‘হোস্টেল’ না বলে ‘হল’ বলাটা আমার কাছে একটু কনফিউজিং লাগে। ফাইনাল পরীক্ষার সময় অ্যাডমিট কার্ড কোথা থেকে নিতে হবে, তা জানার জন্য হলের অফিসে গিয়ে বলতাম, “অ্যাডমিট কার্ড কি হল থেকে নিতে হবে?” কর্মচারীদের একজন বলতেন, “না, না। হলে গেলেই দিয়ে দেবে।” মানে আমি ‘হল’ বলতে বুঝিয়েছি ছাত্রাবাসের অফিস, আর ওই কর্মচারী বুঝিয়েছেন পরীক্ষার হল (ডিপার্টমেন্টে যেই রুমে বসে পরীক্ষা দিতে হবে)।
যাকগে, আমি ভর্তি হওয়ার সময় ছেলেদের ৭টি ও মেয়েদের ৫টি হল ছিল। এখন মনে হয় যথাক্রমে ৮ আর ৭ (অথবা ৮ আর ৬, ঠিক শিওর না)। বিভিন্ন হলে রুমের আকৃতি বিভিন্ন হতে পারে। কোথাও এক রুমে চারজনের সীট, কোথাও তিন জনের, কোথাও দুই জনের। ঢাকায় পরিবার সহ বসবাস করলে আলাদা কথা। কিন্তু নিরাপত্তা ও সাশ্রয়ের জন্য হলে থাকার কোনো বিকল্প আমি পাইনি। সারা দেশ জ্বলে পুড়ে গেলেও শহর থেকে দূরে অবস্থিত, গাছগাছালিতে ঘেরা এই ক্যাম্পাসে তার কোনো আঁচ পাওয়া যায় না। দেশ অচল হয়ে থাকলেও ছাত্রছাত্রীরা হল থেকে আসা যাওয়া করে ক্লাস-পরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারবে, যদি শিক্ষকরা আন্তরিক থাকেন। খাওয়াদাওয়া সহ অন্যান্য খরচ একেবারেই সস্তায় ও নির্ঝঞ্ঝাটে সেরে ফেলা যায়। সাভারে বা ক্যাম্পাসের পেছনের এলাকাগুলোতে বাসা/রুম/মেস নিলে এই সুবিধাগুলোর কোনো কোনোটি পাওয়া যায় না। গণরুমে থাকাকালীন পড়ালেখার অসুবিধা হলে হলের রিডিং রুমে গিয়ে পড়তে বসা যায়। অথবা (বিশেষ করে হলে রিডিং রুম না থাকলে) সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে গিয়েও আরামসে পড়ালেখা করা যায়। রুম পাওয়ার পর ফ্রী খাট, টেবিল, চেয়ার, বুকশেলফ আর লকার তো আছেই। সব মিলিয়ে হলে থাকার সুবিধাটা একটা ব্লেসিং। অনেকের মাস্টার্স শেষ হয়ে গেলেও তাই প্রশাসনের ঠেলা খাওয়া ছাড়া সহজে হল ছাড়তে চায় না ভালো কোনো চাকরি পাওয়ার আগ পর্যন্ত। তাই আমার মতে, গণরুমের কষ্টটা দাঁতে দাঁত চেপে কিছুদিন সহ্য করে নিয়ে হলে পার্মানেন্ট হয়ে যাওয়াই উচিত।
যত ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়, তত সীট হলে নেই। প্রশাসন চাইলে আস্তেধীরে হলেও নতুন নতুন হল তৈরি করে একশ পার্সেন্ট আবাসিক হতে পারবে (এরই ধারাবাহিকতায় ছেলেদের হল সংখ্যা ৭ থেকে ৮-এ এসেছে)। বিভাগের এক শিক্ষককে উষ্মা প্রকাশ করতে শুনেছিলাম, “হলের পর হল বানিয়ে ভার্সিটিটাকে বস্তি বানিয়ে ফেলছে।” আমি তাঁর সাথে দ্বিমত করছি। তিনি ছাত্রজীবনে হলে থাকেননি, তাই এই ব্যাপারে তিনি কোনো জাজমেন্ট না দিলেই ভালো হতো। আমি নিজের অবজার্ভশানের বেশিরভাগ অংশ জুড়েও শুধু একটি হলই থাকবে, যেটায় আমি থেকেছি। মেয়েদের হল বা ছেলেদের অন্যান্য হলের মূল্যায়ন একটু কমই থাকবে।
সীট সংকটের কারণেই হল লাইফ আলোচনা করতে গেলে শুধু গণরুমের কথাই মাথায় আসে। চূড়ান্ত ভর্তি তালিকা হয়ে যাবার কিছু পরই নোটিস দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় কে কোন হলে ‘সীট’ বরাদ্দ পেয়েছে। সীট মানেই এখানে গণরুম। তো গণরুমের পক্ষে-বিপক্ষে নানা রকমের কথা আছে। গণরুমে থেকে ব্যাচমেটদের মধ্যে যে ইন্টিমেসি তৈরি হয়, আগেভাগে সবাই আলাদা আলাদা রুম পেয়ে গেলে তা সম্ভব হতো না–সত্য কথা। গণরুম লাইফ হলো ভার্সিটি লাইফের সবচেয়ে এনজয়েবল টাইম–…হ্যাঁ, কারো কারো বা অনেকের ক্ষেত্রেই সত্য কথা। গণরুম থেকে অনেক লাইফ লেসন পাওয়া যায়–ব্যাখ্যাসাপেক্ষে সত্য।
তবে পাথরশীতল বাস্তবতা হলো, গণরুম একটি সমস্যার ফলাফল। সীট সংকট সমস্যা। সমস্যা গণরুমের বাবা, সমস্যা গণরুমের মা। গণরুম হলো সমস্যার সন্তান। এখন সমস্যা যেহেতু আছেই এবং তা সহসা সমাধান করা যাচ্ছে না, তাই অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ এই সমস্যার অনেক ভালো দিক আবিষ্কার করে নিয়েছে। বেঁচে থাকার তাগিদেই। (এই পয়েন্টটা সামনের পর্বগুলোতে আরো কয়েকবার আসবে ইনশাআল্লাহ।) এই সমস্যার অস্তিত্ব না থাকলে যেচে পড়ে কেউ গণরুম সৃষ্টি করে ইন্টিমেসি বাড়াতে আগ্রহী হতো না।
অভিভাবকরা সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান পড়ালেখা করানোর উদ্দেশ্যে, ইন্টিমেসি-ফিন্টিমেসি এইসব জিনিসের জন্য না। বড়ভাইরা কানপড়া দেয় যে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ালেখা করতে হয় না (তাবলিগি ভাইরাই কেবল বিপরীত কথা বলতেন)। কেউ লাইব্রেরিতে গেলে বা টিউটোরিয়াল (ক্লাসটেস্ট) ছাড়া এমনিই পড়তে বসলে তাকে nerd হিসেবে দেখা হয়। ফলে ফার্স্ট ইয়ারে অনেকের রেজাল্ট খারাপ হয়, পুরো CGPA-তে এর প্রভাব পড়ে। তার উপর একই বয়সের, অবিবাহিত, অভিভাবকের নজরদারীবিহীন কিছু তাগড়া তরুণ-যুবক এক জায়গায় হয় বলে তাদের জঘন্যতম ফ্যান্টাসির সবকিছু বের করে আনে। ছেলে কেমন আছে দেখার উদ্দেশ্যে একজন মা যদি হঠাৎ একদিন চুপিচুপি গণরুমে যান, দেয়ালের লেখা আর ছবিগুলো দেখেই বমি করে ফেলবেন।
ছাত্রদের কে কোন রুম পাবে, তা হল প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে না। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন (‘পলিটিক্যাল’ নামে পরিচিত) এই দিকটা দেখে। (অবশ্য মেয়েদের হলের বিষয়টি আমার ঠিক জানা নেই, ছাত্ররাজনীতির মতো ছাত্রীরাজনীতি অত বেশি প্রভাবশালী না)। কিছু ছেলে নিজের ইচ্ছায় বা অভিভাবকের পরামর্শে গণরুমে নিয়মিত না থেকে কিছু ব্যাগপত্র রেখে ঢাকার বাসায় বা মেসে চলে যায়। ভাবে ব্যাচমেটরা যখন রুম পাবে, সেদিন এসে কোনো একটা রুমে উঠে যাবে। এভাবে হয় না।
পরের বছরের অ্যাডমিশান টেস্ট যখন ঘনিয়ে আসে, তখন দুইজনের রুমে আটজন ঠেসে দিয়ে হলেও গণরুমের নিয়মিত সব বাসিন্দাকে রুম দিয়ে দেওয়া হয়। এটাই রুম পাওয়ার প্রথম ধাপ। এখন যারা গণরুমে থাকেনি, পলিটিক্যালরা যাদের চেনে না, তারা এই প্রক্রিয়ায় রুম পাবে না। পরে এসে যদি সে কারো সুপারিশে রুমে উঠতে পারেও, ব্যাচমেটদের সাথে সে অন্য সবার মতো মিশতে পারবে না। গণরুমে কষ্ট করে থেকে আসা ছাত্ররা তার আরামে রুম পেয়ে যাওয়াকে ভালো চোখে দেখে না এবং জীবনভর এ নিয়ে সামনে-পেছনে খোঁটা মারে। এ ছাড়া গণরুমের সবার মাঝে একটা set of behavior তৈরি হয়ে যায়, যার সাথে পরে হলে ওঠা ছাত্ররা খাপ খাওয়াতে পারে না। এই জিনিসটাই “ম্যানার না জানা” নামে পরিচিত। এই ম্যানার শেখানো নিয়ে পরের পর্বগুলোতে আরো কথা আসবে ইনশাআল্লাহ।
আমি যেই হলে ছিলাম, সেখানে এক রুমে দুইজনের সীট। সর্বপ্রথম সেসব রুমে ছয়জন করে উঠেছিলাম। সবার মুখে একটু একটু খুশির আভা। পলিটিক্যালদের খুশি করতে পারা-না পারার ভিত্তিতে আরো ওঠানামা চলতো। যেমন- কারো আচরণে নাখোশ হয়ে তাকে আবার গণরুমে পাঠিয়ে দিয়ে গণরুম থেকে আরেকজনকে রুমে তোলা। এভাবে একসময় পুরো ব্যাচই রুম পেলো। রুম সংখ্যা একই আছে। তবে এখন প্রতি রুমে আট বা নয়জন। একই ব্লকে পাশাপাশি কয়েকটি রুমে ব্যাচের সবাই। একেকটা মিনি গণরুম। গণরুমের চেয়েও বেশি কষ্টের জীবন। অনেকে মাসজিদে গিয়ে ঘুমাতো, আমিও ঘুমাতে যেতাম মাঝেমাঝে। তাবলিগের ভাইরা আমাদের দেখাশোনা করতেন। (ইতিকাফ বা সফর অবস্থায় না থাকলে নর্মালি মাসজিদে ঘুমানো জায়েয না। তবে চরম পরিস্থিতিতে ফাতওয়ায় কিছু শিথিলতা আসে।) কনকনে শীতকালে গণরুমে গাদাগাদি করতে সমস্যা হতো না। আট-নয়জনের রুমে উঠতে উঠতে গরমকাল চলে এসেছে, কেউই তখনও ফ্যান কেনেনি। অন্য সবাই চালাক-চতুর, বাপ-মা’র ছায়া ছাড়াও জীবনে অনেক জায়গায় থেকেছে, ঘুরেছে। আমি সেরকম না। আমার আব্বা তাই লাইট-ফ্যান সব কিনে এনে কর্মচারী দিয়ে আমাদের রুমে লাগিয়ে দিয়ে গেলেন। অন্য রুমের বাসিন্দারা শেয়ারে ফ্যান কিনে আনার আগ পর্যন্ত পুরো হলের ৪২ তম ব্যাচ আমাদের রুমে এসে দুপুরে আর রাতে ঘুমাতো। এই লাইট আর ফ্যান দিয়ে আমি আজীবন রুমমেটদের উপর ফাঁপড় নিয়েছি। কিছু নিয়ে কোনো রুমমেটের সাথে ঝগড়া লাগলেই আমি লাইট আর ফ্যানের দিকে দেখাতাম আর প্রতিপক্ষ হার মেনে মাফ চেয়ে নিতো।
তখনও আমাদের রুম পাওয়া-না পাওয়া পলিটিক্যালদের হাতে। সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পর এক সময় ওই ব্লক থেকে আমাদের সরিয়ে এনে অন্য আরেকটা ব্লকে আবারও এক রুমে ছয়জন করে রুম দেওয়া হলো। আমাদের রুমে ছাত্রদলের একজন অ্যাক্টিভ কর্মী ছিল বলে তাকে অবশ্য হল থেকে বের করে দেওয়া হয়। তাই আমরা পাঁচজন থাকতাম। এবার যে যার মতো স্বাধীন। যে যার বড় ভাইয়ের সাথে লিংক করে সিঙ্গেল সীটে উঠতে পারে, সে সেই রুমে উঠবে। জেলার বড় ভাই, ডিপার্টমেন্টের বড় ভাই, সাংবাদিক বড় ভাই, তাবলিগের বড় ভাই, সংগঠনের বড় ভাই ইত্যাদি। ব্যাচ থেকে যারা ছাত্রলীগে নাম লিখিয়েছে, তারা উঠে গেলো দোতলায় পলিটিক্যাল ব্লকে। সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে সাংবাদিকরা সবার আগে রুম পেয়েছে সাংবাদিক বড় ভাইদের সাথে লিংক করে। রাজনীতিবিদরা সাংবাদিকদের একটু সমঝে চলে বলে তাদের একটু এক্সট্রা সুবিধা তো থাকবেই! আমি সিঙ্গেল সীট পাই থার্ড ইয়ারের শুরুর দিকে। আমার লিংক ছিল তাবলিগ। তাবলিগের মাশোয়ারার ভিত্তিতে আমাদের ব্যাচ থেকে দুইজন রুম পাই। দুই ব্যাচমেট অবশ্য একই রুমে না। দুইজন দুই সিনিয়র ভাইয়ের সাথে দুই রুমে। একেবারে মনের মতো রুম। নামাজি, দাড়িওয়ালা, সুন্দর আখলাকসম্পন্ন, নন-স্মোকার রুমমেট। সবচেয়ে বড় কথা, রুমমেট নাট্যতত্ত্ব বিভাগের না। নিচতলায় আটজন-ছয়জনের রুমে থাকতে নাট্যতত্ত্বের পোলাপান বহুত জ্বালাতন করত।
এখানে বলে রাখা ভালো যে “সাংবাদিকদের রুম”, “তাবলিগের রুম”, “অমুক সংগঠনের রুম” বলে আলাদা কিছু নেই। শুধু পলিটিক্যালরাই দোতলার দুই-আড়াই ব্লক জুড়ে চিরস্থায়ীভাবে থাকে, যেগুলো পলিটিক্যাল ব্লক নামে পরিচিত (আমাদের হলে তারা দোতলায় থাকে, অন্যান্য হলের নিয়ম জানি না)। সরকার পরিবর্তন হলে ওই দলের ছাত্ররা এদের তাড়িয়ে দিয়ে এই রুমগুলোতেই ওঠে। এগুলো ফিক্সড। কিন্তু অন্যান্যরা যেসব রুমে থাকে, তারা নিজ নিজ সংগঠনের জন্য রুমগুলো আন-অফিশিয়ালি ধরে রাখে। অর্থাৎ, হল ছেড়ে চলে যাবার সময় নিজ সংগঠন বা জেলার জুনিয়রকে রুম দিয়ে যাওয়া। এভাবেই তাবলিগের রুমগুলোতে তাবলিগিরাই ওঠে, ছাত্র ইউনিয়নের রুমে ছাত্র ইউনিয়ন ওঠে, কোনো জেলা সমিতির সভাপতির রুমে ওই জেলা সমিতির পরবর্তী সভাপতি ওঠে…ইত্যাদি।
আরেকটা কথা হলো যেকোনো নামাজি-দাড়িওয়ালা ছেলেই যে তাবলিগের রুমে উঠে যেতে পারবে, এমন কথা নেই। প্র্যাক্টিসিং মুসলিম, কিন্তু আহলে হাদীসের কোনো গ্রুপের সাথে জড়িত অথবা নির্দিষ্ট কোনো দলের সাথেই জড়িত না, এমন ছেলেদের আবার তাবলিগের রুমে তোলা হয় না। ক্যাম্পাসে আসার আগে বা পরে তাবলিগের মেহনতে সময় দিয়েছে, এমন ছেলেরাই উঠতে পারে।
তো এভাবেই রুম পেতে হয় আরকি। যারা কোনো না কোনো বড় ভাইয়ের সাথে শক্ত লিংক করতে পারে না, তাদের সিঙ্গেল সীট পেতে পেতে অনার্সও শেষ হয়ে যায় অনেকের। তবে এদের সংখ্যা কম।
হল প্রশাসনের কাজ হলো মাস-দুমাসে একবার রাতের বেলা সব স্যাররা মিলে কাগজ হাতে নিয়ে ‘রুম লিস্ট’ করতে বের হওয়া। কর্মচারীরা আগে আগে গিয়ে রুমে নক করে বলে আসে, “স্যাররা আসতেছে। রেডি হন।“ স্যাররা এসে রুমে কে কে আছে জিজ্ঞেস করেন, নাম, ব্যাচ, রোল লিখে নেন। কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না জিজ্ঞেস করে উত্তরের অপেক্ষা না করে পরের রুমে চলে যান। তবে মাস্টার্স পরীক্ষা শেষেও পলিটিক্যাল ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ ছাত্র হলে অবস্থান করছে, এরকম দেখতে পেলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তাকে হল ছাড়তে আদেশ দেন। মাঝেমাঝে ছাত্ররা মুখের উপর বলে দেয়, “স্যার, এখন চাকরির পড়াশোনা আছে। হল ছাড়তে পারবো না। তিন-চার বছর পর রুম পাইসি, আপনারা তখন কোনো ব্যবস্থা নেননাই।”
ছেলেদের হলগুলোতে নিয়ম হলো মাস্টার্স পরীক্ষার ভাইভা অথবা থিসিসের ডিফেন্স শেষ করার এক সপ্তাহের মাঝে হল ছাড়তে হবে। সাধারণ ছাত্ররা বিসিএসে উত্তীর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত (বা অন্তত প্রিলি দেওয়া পর্যন্ত) থাকার চেষ্টা করে। কেউ মাস্টার্স শেষে দেড়-দুই বছর থাকার পর প্রশাসনের চাপাচাপিতে হল ছাড়তে বাধ্য হয়। আর পলিটিক্যালরা লাইফটাইম হলে থাকতে পারে, যদি না মাঝখান দিয়ে সরকার চেইঞ্জ হয়ে যায়। আমার পুরো ভার্সিটি লাইফে একবারও সরকার পাল্টায়নি দেখে অনেককেই দেখেছি ১০-১২ বছর হলে থাকতে। তাও দুইজনের রুমে একা একজন। তাবলিগের ভাইরা ব্যতিক্রম। তাবলিগের রুমে আমার প্রথম যেই রুমমেট ছিলেন (আমার সিনিয়র), তিনি বৈধ সময়সীমা শেষ হওয়া মাত্রই আরেক জুনিয়র তাবলিগিকে নিজের সীটে তুলে দেন। রাতে মাসজিদে গিয়ে ঘুমাতেন। দিনের বেলা চাকরির বইপত্র নিয়ে এসে ঢুকে বলতেন, “তোমাদের রুমে একটু পড়তে বসি?” কিছুদিন পর বাসা ভাড়া নেয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এভাবে চলেন। এখন তিনি জব করছেন ও বিয়েশাদি করে থিতু হয়েছেন।
হল লাইফের প্রসঙ্গের টানে টানে র্যাগিং এবং ক্যাম্পাসের খানাদানা, পরিবেশ, পলিটিক্স অনেককিছুই চলে আসার কথা। পরবর্তী কোনো পর্বে হবে ইনশা আল্লাহ।
মুসলিম মিডিয়া ব্লগের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সহ তা সামনের দিকে এগিয়ে নিতে আপনার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। ব্লগ পরিচালনায় প্রতি মাসের খরচ বহনে আপনার সাহায্য আমাদের একান্ত কাম্য। বিস্তারিত জানতে এখানে ভিজিট করুন।
নিচে মন্তব্যের ঘরে আপনাদের মতামত জানান। ভালো লাগবে আপনাদের অভিপ্রায়গুলো জানতে পারলে। আর লেখা সম্পর্কিত কোন জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে অবশ্যই "ওয়ার্ডপ্রেস থেকে কমেন্ট করুন"।